আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা গদ্যসাহিত্য | Class 11 Second Semester WBCHSE
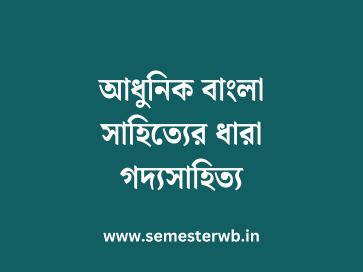
১। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্কারের ফলশ্রুতি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ।’-মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।
বাংলায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের • সময়পর্বকেই ‘নবজাগরণের কাল’ বলা হয়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬১) • পর থেকে মূলত বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটে। অবশ্য অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ১৭৫৭ সালে এক গতিশীল জাতির হাতে স্থিতিশীল আর-এক জাতির পরাজয়ের মধ্যেই বাংলায় আধুনিকতার অস্ফুট সূত্রপাত। এ বিষয় নিয়ে মতবিরোধ আছে। ‘কালের পুতুল’ গ্রন্থে কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন-“আধুনিক কথাটির সংজ্ঞার্থ যুগে যুগে বদলায়। অভিনবত্বের আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী এবং সর্বশেষ বিচারে বোধহয় এ কথাই বলতে হয় যে সেইটিই সত্যিকারের আধুনিক, যেটা চিরন্তন।” রবীন্দ্রনাথ ‘আধুনিক’ শব্দটিকে কালের দিক থেকে বিচার করতে চাননি। তিনি ‘আধুনিক কাব্য’ প্রবন্ধে লিখেছেন- “পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। সেটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাববার কথা।” আধুনিক বা আধুনিকতার চরিত্র পরিবর্তিত হয়। মানুষের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক বা আধুনিকতার চরিত্র পরিবর্তিত হয়।
বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগগত লক্ষণ
১. আত্মপ্রত্যয়ের সুর ও অনিশ্চয়তার সমস্যা। ২. দেবতা নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ব্যক্তিমানুষের গুরুত্ব আরোপ। ৩. আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও বিপ্লবের প্রতিফলনস্বরূপ সমাজতন্ত্র ও অর্থনীতিকে নতুন চেতনায় আলোড়িত করেছে মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী মানুষের হৃদয়। ৪. বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব আধুনিক সাহিত্যের সার্বিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ৫. ইউরোপীয় জীবনের প্রভাব বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতো আছড়ে পড়েছে বাঙালির চিন্তাচেতনায়। ৬. অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সেই প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেনি।
সময়ের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় আধুনিকতার বিকাশ ঔপনিবেশিক সমাজে সামন্তবাদ যখন পুরোনো ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছিল, তখনই উপনিবেশবাদ ধনতন্ত্রের যে নতুন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল তারই প্রতিফলনে আধুনিকতার বিকাশ শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা কবিগানে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। আত্মদ্বন্দু আর স্ববিরোধিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতায় পথচলা শুরু বলা যেতে পারে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাবে বহু স্মরণীয় গ্রন্থ রচনায়, সভাসমিতির প্রতিষ্ঠায়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ও প্রসার ঘটে। শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের হাত ধরে যুক্তিমনস্কতার মাধ্যমে কুসংস্কার দূরীভূত হয়। মহাবিদ্রোহের পর বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জোয়ার আসে। কাব্য, উপন্যাস, নাটক রচনায় ফুটে ওঠে যথার্থ আধুনিকতা।
২। দিগদর্শন’ থেকে ‘বঙ্গদর্শন’ পর্যন্ত সমসাময়িক পত্রের ধারা পর্যালোচনা করলে কোন্ তথ্য উঠে আসে? দিগদর্শন পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল, সম্পাদকের নাম ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব লেখো।
‘দিগদর্শন’ (১৮১৮) থেকে ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭২) পর্যন্ত সমসাময়িক পত্রের ধারা পর্যালোচনা করলে যানা যায়-সমাজ-রাজনীতি-ধর্ম-দর্শন-শিক্ষা সম্পর্কিত যুক্তিনিষ্ঠ ও নীতিনির্ভর প্রবন্ধ-কবিতাই আলোচ্য কালপর্বে রচিত হয়েছে। গদ্য ক্রমশ কাঠিন্য ও নীরসতা বর্জন করে সরস ও সর্বজনবোধ্য হয়ে উঠেছে।
১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রীরামপুর মিশনারিদের পরিচালনায় জে সি মার্শম্যান-এর সম্পাদনায় দিগদর্শন ‘মাসিক’ পত্রিকা হিসেবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়।
দিগদর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
প্রথম বাংলা সমসাময়িক পত্রিকা হিসেবে দিগদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে যুবকদের মানসিক উৎকর্ষসাধনের জন্য তথ্য ও উপদেশ সংবলিত এই পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। এতে ছাত্রদের উপযোগী ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করা হত। ‘স্কুল বুক সোসাইটি’ এই পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যা বহু কপি ক্রয় করত। ১৮১৮ সালের সময়কার কৌতূহলোদ্দীপক প্রসঙ্গগুলি পত্রিকাতে সযত্নে ঠাঁই পেয়েছে। বহু প্রতিকূলতা দেখা দেওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
৩। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা প্রথম কে, কবে সম্পাদনা করেন? পরবর্তী পর্যায়ে সম্পাদক ও লেখকগোষ্ঠীর পরিচয় দিয়ে বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব লেখো।
১৮৭২ সালে (১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ) সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘বঙ্গদর্শন’ প্রথম প্রকাশিত হয়।
‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার পরবর্তী পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায়
(১২৮২-১২৮৯)- সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক) ও তৃতীয় পর্যায় (১২৯০ কার্তিক-মাঘ)- শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক)। পত্রিকাটি বেশ কিছুকাল বন্ধ থাকার পর আবার চতুর্থ পর্যায়ে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায়।
(1) বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী: রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।
(2) ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার উদ্দেশ্য: বঙ্গদর্শনের প্রথম সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজে লিখেছেন- “এই পত্রিকা আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙালি সমাজে ইহা তাহাদিগকে বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকার্যের পরিচয় দিক। ইহা বঙ্গ মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সাহিত্য আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সংবর্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।”
ব্রাহ্মগোষ্ঠী বহির্ভূত যেসব নব্য শিক্ষিত বাঙালি ধর্মীয় আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন, তাঁরা নবযুগের সাধনার বাণী থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এইসব শিক্ষিত বাঙালিদের কাছে পৌঁছোনো ছিল বঙ্গদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য।
(3) ঐতিহাসিক গুরুত্ব: (১) ‘বঙ্গদর্শন’ উনিশ শতকের বাঙালির প্রাণের ক্ষুধা ও হৃদয়ের পিপাসা নিবৃত্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। (২) সমকালীন যুগের বাণীকে প্রতিফলিত করতে বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও মনীষীদের সংঘবদ্ধ করেছিল। (৩) জাতীয়তাবোধ ও স্বজাতি প্রীতির প্রকাশ ঘটেছিল পত্রিকায়। (৪) ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকাকে ঘিরে জন্ম নেওয়া বেশ কিছু সাহিত্যিক পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে বঙ্গদর্শনের অবদান ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ।
৪। ‘সবুজপত্র’ পত্রিকাটির পরিচয় সহ ‘সবুজপত্র গোষ্ঠী’-র অন্তর্ভুক্ত কারা ছিলেন উল্লেখ করো। রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ রচনা সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?
অথবা,
সমসাময়িক পত্রিকা হিসেবে সবুজপত্রের ভূমিকা লেখো।
বীরবল ছদ্মনামে প্রমথ চৌধুরী ১৯১৪ সালে মাসিক পত্রিকা ‘সবুজপত্র’ প্রথম সম্পাদনা করেন।
(1) সবুজপত্রের উদ্দেশ্য: সাহিত্যে গণচেতনা ও জন-অধিকার, রচনার ক্ষুদ্রত্ব, সাহিত্যসেবা, বেনিয়াবৃত্তির উপায়, কৃত্রিমতা ও ভাবাবেগের তারল্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি রচিত। মননশীল সাহিত্যরচনার মহৎ আদর্শ সৃষ্টি করার জন্যও পত্রিকাখানি প্রকাশ করা হয়েছিল।
(2) ‘সবুজপত্র গোষ্ঠী’: ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার মুখবন্ধে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন-“ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে সাহিত্যের ফুল ফুটেছে। তার ফল কি হবে সে-কথা না বলতে পারলেও এই ফুল ফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন তাঁকেই ফুল চাষ করবার জন্য উৎসাহ দেবে। আমরা এই নতুন পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি। এটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালির জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য।” প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কবিকন্যা মাধুরীলতা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বরদাচরণ গুপ্ত, বীরেশ্বর সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন এর লেখকগোষ্ঠী।
রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছোটোগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য-
- ছোটোগল্প : ‘হালদার গোষ্ঠী’, ‘হৈমন্তী’, ‘বোষ্টমী’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘ভাইফোঁটা’, ‘শেষের রাত্রি’, ‘অপরিচিতা’, ‘তপস্বিনী’, ‘পয়লা নম্বর’, ‘পাত্র ও পাত্রী’ প্রভৃতি।
- উপন্যাস: ‘ঘরে বাইরে’, ‘চার অধ্যায়’।
- প্রবন্ধ: ‘কালান্তর’, ‘বাতায়নিকের পত্র’ প্রভৃতি।
৫। বাংলা সাহিত্যে ‘কল্লোল’ পত্রিকার ভূমিকা আলোচনা করো।
অথবা,
‘কল্লোল’ পত্রিকাটির পরিচয় দিয়ে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব লেখো।
১৯২৩ সালে দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগের সম্পাদনায় ‘কল্লোল’ পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় (মাসিক পত্রিকা)।
(1) কল্লোলের লেখকগোষ্ঠী: ‘কল্লোল’ পত্রিকার লেখকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এ ছাড়া, বিভিন্ন লেখিকারাও ‘কল্লোল’ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-রাধারাণী দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, নীলিমা বসু, সরোজকুমারী দেবী, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতি দেবী প্রমুখ।
‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর লেখকেরা মনে করতেন যে, পৃথিবীতে একটা আর্থসামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। সেইসঙ্গে সাহিত্যের চিন্তাভাবনারও পরিবর্তন ঘটা প্রয়োজন। ১৯২১ সালে ভারতে গান্ধিজির আন্দোলনের ব্যর্থতা, রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠা শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রয়েডের চিন্তাধারা সাহিত্যিকদের মনোজগৎকে আলোড়িত করেছিল। ‘কল্লোল’ তার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিল সাহিত্যের মাধ্যমে। তাই তাঁরা রবীন্দ্র বিরোধিতা করে নবযুগ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।
(2) ঐতিহাসিক গুরুত্ব : (১) কলকাতা ও ঢাকার শিক্ষিত যুবকদের দুঃসাহসিকতার ফলশ্রুতি ‘কল্লোল’। (২) বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবে আবির্ভূত ও আধুনিকতার প্রতি অনুরক্ত। (৩) ‘বাস্তববাদী’ গোকুলচন্দ্র নাগের বাস্তববাদী উপন্যাস ‘পথিক’-কে আধুনিক উপন্যাসের স্বরূপ অভিহিত করা হয়। (৪) বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের খ্যাতিমান অনেক কবি ও সাহিত্যিকের সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রভূমি কল্লোল। (৫) ফ্রয়েড ও মার্কসকে অবলম্বন করে বাস্তব, আধুনিক চিন্তাদর্শনে সমৃদ্ধ সাহিত্যরচনা।
৬। বাংলা গদ্যের বিকাশে ‘শ্রীরামপুর মিশন’-এর অবদান লেখো।
বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান অবিস্মরণীয়। প্রধানত বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্যই কলকাতার নিকটবর্তী হুগলির শ্রীরামপুরে এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন খ্রিস্টান মিশনারিরা। এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারই ছিল এই মিশন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য।
বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান-
(1) ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা: ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আসা ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরি, ১৭৯৯ সালে গ্র্যান্ট, বার্নসডন, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপলব্ধি করেছিলেন বঙ্গদেশে ছাপাখানা প্রয়োজন। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশনে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা। ১৮০১ সালে এই ছাপাখানা থেকে ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’, ১৮০২ সালে ‘কাশীদাসী মহাভারত’ ছাপা হয়।
(2) বাইবেলের অনুবাদ: শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন এবং শ্রীরামপুর মিশন মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের ওপর গুরুত্বদান করেন। বাইবেল বহু ভাষায় অনূদিত হয়। খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারলাভ করে বঙ্গদেশে।
(3) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ: শ্রীরামপুর মিশনে প্রথমদিকে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হলেও ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠান থেকে গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ, ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ, ‘দি গসপেল অফ সেন্ট’ ম্যাথ্যুর অনুবাদ মঙ্গল সমাচার, মতিউর রচিত বাইবেলের অনুবাদ, ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৩১), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮) শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। ‘সমাচার দর্পণ’ নামে সাপ্তাহিক এবং ‘দিগদর্শন’ নামে মাসিক পত্রিকাও এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়।
মন্তব্য
শাসনকর্মের সুবিধা ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া শ্রীরামপুর মিশন বাংলা গদ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বাঙালির মনের মাধুরী মিশ্রিত রামায়ণ, মহাভারত গ্রন্থ বাংলায় এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হলে বাঙালির হৃদয়ের খোরাক মেটে। গদ্যসাহিত্যের বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।
৭। বিদ্যাসাগরের মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থের নাম লেখো এবং গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য লেখো।
‘বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।’ তাঁর প্রথম রচনা ভাগবত অবলম্বনে রচিত ‘বাসুদেবচরিত’ (অপ্রকাশিত)। তবে তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনার নাম ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ (১৮৪৭)। গ্রন্থটি হিন্দি ‘বৈতাল পচ্চীসীর’ অনুবাদ।
(1) বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থ : (১) ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৩), (২) ‘বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৫), (৩) ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার’ (১৮৭১), (৪) ‘অতি অল্প হইল’ (১৮৭৩), (৫) ‘আবার অতি অল্প হইল’ (১৮৭৩), (৬) ‘ব্রজবিলাস’ (১৮৮৪), (৭) ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’ (১৮৬৩), (৮) ‘বিদ্যাসাগর চরিত’ (১৮৯১)।
(2) বিদ্যাসাগরের অনূদিত গ্রন্থ : (১) ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ (১৮৪৭) [বৈতাল পচ্চীসীর অনুবাদ], (২) ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ (১৮৪৮) [মার্শম্যানের ‘History of Bengal’-এর অনুবাদ], (৩) ‘জীবনচরিত’ (১৮৪৯) [চেম্বার্সের ‘Biographies’-এর অনুবাদ], (৪) ‘বোধোদয়’ (১৮৫১) [চেম্বার্সের ‘Rudiments of Knowledge’-এর অনুবাদ], (৫) ‘শকুন্তলা’ (১৮৫৪) [কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ অনুবাদ], (৬) ‘কথামালা’ (১৮৫৬) [ঈশপের ফেবলসের অনুবাদ], (৭) ‘সীতার বনবাস’ (১৮৬০) [ভবভূতির ‘উত্তরচরিত’-এর কিছু অংশের অনুবাদ], (৮) ‘ভ্রান্তিবিলাস’ (১৯৬৯) [শেক্সপিয়রের ‘Comedy of Errors’-এর অনুবাদ]
(3) বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য: (১) সমাসবহুল দীর্ঘ বাক্যের পরিবর্তে ছোটো বাক্য ব্যবহার করে বোধগম্যতা বাড়িতে তুলতে চেষ্টা করেছেন। (২) ছেদ, যতি চিহ্নের প্রয়োগ করে বাংলা গদ্যকে শিল্প সৌকর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। (৩) তাঁর সাধু গদ্যে সংযুক্ত হয়েছে শিল্পীমনের সংযম ও পরিমিত বোধ। (৪) তাঁর গদ্যরীতি প্রাণস্পন্দনে পরিপূর্ণ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। (৫) তিনি সাধুগদ্যকে সমর্থন করেছেন। তাঁর গদ্য ভাষা কৈশোরের অনিশ্চয়তা ও অস্থির গতি ছেড়ে যৌবনের পূর্ণ সাহিত্যিক রূপে স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
৮। বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা করো।
“বাংলা গদ্য তাঁর হাতে আয়ুধে পরিণত হয়েছিল। সুললিত সাহিত্যিক গদ্য তাঁর ততটা আয়ত্তে না এলেও গুরুতর তত্ত্বালোচনায় গদ্যকে ব্যবহার করে তিনি বিতর্ক ও বিচারের সংযত ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। এইজন্য তিনি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দিকনির্দেশক স্মারকস্তম্ভ রূপে দীর্ঘকাল বিরাজ করবেন।” -অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
‘ভারতপথিক’ রামমোহন রায় বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে ধ্রুবতারা। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের শৈশবকালে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যকে ব্যবহার করেন। ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতির কথা তিনি গদ্যে আলোচনা করে তার শক্তি প্রকাশ করলেন। ধর্মসংস্কার ও সমাজচেতনার বশবর্তী হয়েই রামমোহন গদ্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।
(1) গ্রন্থসম্ভার: বহুভাষী, পণ্ডিত রামমোহন রায় আরবি-ফারসি ভাষায় একেশ্বরবাদ বিষয়ে প্রথম রচনা করেছিলেন ‘তুহফাৎ উল-মুয়াহহিদীন’ (১৮০৩)। তবে বাংলায় একেশ্বরবাদ সমর্থনে তাঁর প্রথম রচনা ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ (১৮১৫) ও ‘বেদান্তসার’ (১৮১৫)। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য-
- ধর্ম ও তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা: ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’ (১৮১৭), ‘গোস্বামীর সহিত বিচার’ (১৮১৮), ‘কবিতাকারের সহিত বিচার’ (১৮২০), ‘ব্রাহ্মণ সেবধি’ ও ‘মিশনারি সম্বাদ’ (১৮২১), ‘চারি প্রশ্নের উত্তর’ (১৮২২), ‘পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ’ (১৮২৩) প্রভৃতি।
- শাস্ত্র সমর্থিত আচার ব্যবহার সম্পর্কিত মৌলিক রচনা: ‘উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার’ (১৮১৮), ‘সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্ত্তক সম্বাদ’ (১৮১৮-১৮১৯), ‘সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার’ (১৮২০), ‘পথ্যপ্রদান’ (১৮২৩), ‘কায়স্থের সাথে মদ্যপান বিষয়ক বিচার’ (১৮২৬) প্রভৃতি।
- ব্যাকরণ গ্রন্থ: ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ (১৮৩৩)
(2) পত্রিকা সম্পাদনা : ‘ব্রাহ্মণ সেবধি’ (১৮২১), ‘সম্বাদ কৌমুদী’ (১৮২১), ‘মীরাৎ-উল আখবার’ (১৮২২)
(3) গদ্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য: রামমোহনের গদ্যভাষাকে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন-‘জলবৎ তরল’।
(১) রামমোহনের হাতে তাঁর গদ্য সমসাময়িক সামাজিক চৈতন্যের মধ্যে কল্যাণধর্ম প্রতিষ্ঠার কারণেই হয়ে উঠেছে চিন্তাবাহী, মনন সমৃদ্ধ, যৌক্তিক পারম্পর্যে বিধৃত। (২) তাঁর গদ্য মূলত কর্মযোগীর গদ্য-তাই গদ্যরীতির রসবিলাস বা রোমান্টিক বিন্যাস-কুশলতা থেকে তাঁর গদ্য কিছুটা দূরবর্তী। (৩) তাঁর গদ্যে অনেকাংশে কর্তা ও ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের প্রলম্বিত গঠনরীতির কারণে সম্পর্কসূত্র কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে। (৪) তাঁর গদ্যে ছেদ-যতির যথার্থ প্রয়োগ না-থাকলেও বোধগম্য।
ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে-‘…তাঁহার গদ্য ললিতমধুর না হইলেও > মননদীপ্ত ও ভাবের সমুন্নতিতে মর্যাদাময়।’
৯। অক্ষয়কুমার দত্ত কোন্ পত্রিকা, কবে সম্পাদনা করেছেন? তাঁর রচিত গদ্যগ্রন্থগুলির নাম লেখো ও গদ্যবৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করো।
অথবা,
বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের অবদান লেখো।
১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের মননশীল প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য অক্ষয়কুমার দত্ত। বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছন্দচারিতা তাঁর প্রবন্ধে অনুকরণীয় মননশীলতা এনেছে এবং বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির সার্থক প্রয়োগে তা যথেষ্ট প্রসাদগুণেরও অধিকারী হয়েছে।
গদ্যগ্রন্থসমূহ
(১) ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার’ (১৮৫১, ১৮৫৩), (২) ‘চারুপাঠ’ (প্রথম খণ্ড-১৮৫৩, দ্বিতীয় খন্ড-১৮৫৪, তৃতীয় খন্ড-১৮৫৯), (৩) ‘ভূগোল’ (১৮৪১), (৪) ‘ধর্মনীতি’ (১৮৫৫), (৫) ‘ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৫), (৬) ‘পদার্থবিদ্যা’ (১৮৫৬), (৭) ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ (প্রথম খন্ড-১৮৭০, দ্বিতীয় খন্ড- ১৮৮৩), (৮) ‘প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার’ (১৯০১)।
গদ্যবৈশিষ্ট্য
(১) তাঁর গদ্যে সরসতার অভাব লক্ষ করা যায়। গদ্যের ভাষা সরস যুক্তিবাদের ভাষা। তবে তাঁর গদ্যশৈলী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবনার প্রকাশ সৃজনীশক্তির পরিচায়ক। (২) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, ‘তিনি বাঙালির সর্বপ্রথম নীতি শিক্ষক’। শুধু বিষয় মাহাত্ম্য, গবেষণা প্রয়াস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছাড়াও অক্ষয়কুমার এদিক থেকেও স্মরণীয়। (৩) বিদ্যাসাগরীয় গদ্যশৈলীকে মাধুর্য ও শিল্পসুষমামণ্ডিত করে তুলেছেন যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগে মসৃণ এবং সাবলীলভাবে। (৪) তাঁর সময় থেকেই বাংলা প্রবন্ধ বাদ-প্রতিবাদের পথ ত্যাগ করে এক উক্তিমূলক প্রবন্ধরীতির সূত্রপাত ঘটে। (৫) তাঁর গদ্য মূলত জ্ঞানের সাহিত্য। সেখানে যুক্তির বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার পরিচয় আছে। (৬) পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারাকে বাংলা গদ্যে আনার চেষ্টা করেন। (৭) সংস্কৃতগন্ধী অনেক শব্দকে তিনি বাংলা ভাষায় স্বচ্ছভাবে প্রয়োগ করেছেন।
১০। সাহিত্যিক চলিতরীতির গদ্যের প্রবর্তক কে এবং তাঁর গদ্যভাষা কী নামে পরিচিত? তাঁর গদ্যগ্রন্থ ও গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য লেখো।
অথবা,
প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্যবৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
সাহিত্যিক চলিতরীতির গদ্যের প্রবর্তক হলেন-প্যারীচাঁদ মিত্র (ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর)।
তাঁর গদ্যভাষা ‘আলালী গদ্য’ রীতি নামে খ্যাত হয়ে আছে।
তাঁর গদ্যগ্রন্থসমূহ
প্যারীচাঁদ মিত্রের উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থগুলিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়-
(১) প্রবন্ধমূলক রচনা- ‘কৃষিপাঠ’ (১৮৬১), ‘যৎকিঞ্চিৎ’ (১৮৬৫)।
(২) জীবন আখ্যান-ডেভিড হেয়ারের ‘জীবনচরিত’ (১৮৭৮)।
(৩) কথোপকথনমূলক নীতি আখ্যান- ‘রামারঞ্জিকা’ (১৮৬০), ‘অভেদী’ (১৮৭১), ‘আধ্যাত্মিকা’ (১৮৮০), ‘বামাতোষিণী’ (১৮৮১)।
(৪) সমাজসংস্কারমূলক-‘এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা’ (১৮৭৯)।
(৫) ব্যঙ্গাত্মক নকশা জাতীয় রচনা-‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮), ‘মদ খাওয়া বড়ো দায় জাত রাখার কি উপায়’ (১৮৫৯) ইত্যাদি।
গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য
(১) কলকাতার চলতি বুলি বা কক্সী ভাষার মাধ্যমে কৌতুক রস সৃষ্টি। (২) সাধুভাষা ও কথ্য ভাষার মিশ্রণে একটি সহকর বাচনভঙ্গি তৈরি হয়েছে এই গদ্যরীতিতে। (৩) অধ্যাপক পরেশ ভট্টাচার্য বলেছেন, “বাক্যের গঠনে সাধুরীতি ব্যবহার করতে গিয়েও প্যারীচাঁদ অনেক সময় রীতি লঙ্ঘন করেছেন, ফলে তা কখনও আদর্শ ভাষা হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি।” (৪) সরল বাক্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম কথ্যরীতির প্রচলন করেন। (৫) বাস্তবজীবন চিত্রণে ও গল্পরসের মহিমায় তাঁর গদ্য অনবদ্য।
১১। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থটির রচয়িতা ও প্রকাশকাল লেখো। তাঁর গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য লেখো।
অথবা,
কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যশৈলীর বিশেষত্ব লেখো।
‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। গ্রন্থটির প্রকাশকাল-(প্রথম খন্ড ১৮৬১ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৬২)
গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য
‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’- “এই বই সেকালের কলিকাতা শহরের চলতিভাষায় লেখা। এরকম চতুরগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।”- প্রমথ চৌধুরী।
(১) হুতোমের গদ্য ভাষায় পারস্পরিক শৃঙ্খলতার অভাব লক্ষ করা গেলেও, এই ভাষার সরস গতিপ্রবাহই ‘হুতোমী ভাষা’ রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। (২) হুতোম কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করেছেন, কথ্য ভাষার আটপৌরে স্বভাবকে পর্যন্ত পরিবর্তন করেননি। উচ্চারণভঙ্গিও যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন। (৩) কালীপ্রসন্নের ভাষা একান্তভাবে নকশার ভাষা। হুতোমের কাছে গল্পরস নয়-সমাজের ছবি প্রাধান্য লাভ করেছে। গ্রন্থের ভাষা সেই ছবির একান্ত উপযোগী হয়েছে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, “হুতোমের নকশা বঙ্গসাহিত্যের নূতন গহনা ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি।” (৪) উত্তর ও মধ্য কলকাতার কথ্য বাংলা কক্সি ভাষা তাঁর গদ্যশৈলীর আভিজাত্যকে প্রকাশ করে। (৫) ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-নকশা জাতীয় রচনা। হুতোমের ভাষা চিত্ররচনায় নিপুণ। বলা চলে চিত্র বর্ণবহুল, গতিময়। গ্রন্থটি যেন বর্ণাঢ্য ভাষার চলচ্চিত্র। (৬) বাঙালির সমাজ ও নৈতিক জীবনের সর্বতোমুখী কল্যাণসাধনের কারণেই ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-য় নির্মম ব্যঙ্গের কশাঘাত সুতীব্র হয়ে উঠেছে।
১২। ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ কে রচনা করেন এবং গ্রন্থটিতে কার, কোন্ গ্রন্থের ছায়া আছে? গ্রন্থটিতে বর্ণিত কয়েকটি চরিত্রের নামোল্লেখ করে গ্রন্থটির বিষয় ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।
অথবা,
বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করো।
‘কমলাকান্তের দপ্তর’ গ্রন্থটির রচয়িতা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থটিতে ডি কুইন্সির ‘কনফেসন অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার’-এর ছায়া রয়েছে।
গ্রন্থটিতে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কমলাকান্ত, ভীষ্মদেব খোশনবীশ, নসীরামবাবু, প্রসন্ন গোয়ালিনী প্রমুখ।
গ্রন্থটির বিষয়
‘কমলাকান্তের দপ্তর’ ব্যক্তিধর্মী প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর মনন সমৃদ্ধজাত এই প্রবন্ধে কমলাকান্তের আত্মজীবনীতে প্রকাশ পেয়েছে দার্শনিকতা, সমাজ, রাজনীতি, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি। ১৮৭৫ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট ১৪টি প্রবন্ধ আছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল-একা-কে গায় ওই, মনুষ্যফল, বসন্তের কোকিল, বিড়াল, পতঙ্গ, ঢেঁকি, স্ত্রীলোকের রূপ প্রভৃতি।
(১) বিদ্রূপাত্মক ভাষার শাণিত তীরে এবং উদ্ভট কল্পনার রূপ বিলাসে সামাজিক বিচিত্র অসংগতি উপস্থাপন।
(২) জাতীয় চরিত্রের নানা দুর্বলতাকে তীব্র আঘাত করেছেন।
(৩) সামাজিক বৈষম্য, অবিচার, অত্যাচারকে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ পরিহাসের মাধ্যমে প্রবন্ধগুলিতে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।
বৈশিষ্ট্য
‘কমলাকান্তের দপ্তর’ সৃজনে বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধনহীন শিল্পী ও নির্মল হাস্যরসিক। আবদুল আজীজ আল্ আমান তাঁর ‘সাহিত্যসঙ্গ’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,- “ঋষি এবং নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্রের চাপা ওষ্ঠাধারের অন্তরালে যে হাস্যরসের অফুরন্ত আবেগ ও লঘু চাপল্য লুকিয়েছিল কমলাকান্তের দপ্তর না পেলে আমরা হয়তো কোনোদিনই বিশ্বাস করতাম না। হাসির অনাবিল স্রোতে দোল খেয়ে প্রত্যেকটি কথা ও মন্তব্য একান্ত সজীব এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।”
(১) ভাষার মাধুর্যে, ভাবের মনোহারিত্বে, শুভ্র-সংযত-সরস রসিকতায়, অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে গ্রন্থটি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব। কমলাকান্তের গদ্যরীতি বঙ্গসাহিত্যে অভিনব।
(২) হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের মিশ্রণ।
(৩) ভাবুকতার সঙ্গে বস্তুতন্ত্রতার, তরলতার সঙ্গে মর্মদাহিনী জ্বালার মিশ্রণ।
(৪) শ্লেষের সঙ্গে উদারতার এমন মিশ্রণ বঙ্গসাহিত্যে বিরল।
(৫) বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপম কল্পনাপ্রসূত চার চরিত্র কমলাকান্তের দপ্তরে নিজ নিজ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। কমলাকান্তের মধ্যে একজন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সূক্ষ্মদর্শিতা, চিন্তাশীল পৌরুষের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।
১৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দর্শন ও ধর্মবিষয়ক, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক, হাস্যরসাত্মক, সাহিত্য সমালোচনামূলক কমপক্ষে ২টি করে প্রবন্ধের নাম লেখো ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাশৈলীর বৈশিষ্ট্য লেখো।
বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধসাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট। একদিকে রূপবৈচিত্র্যের চারুশিল্পী অন্যদিকে ভাবসত্তার স্রষ্টা। পূর্বে বাংলা প্রবন্ধ চিন্তা ও মননের বাহন ছিল, যার সীমা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের তথ্য ও তত্ত্বের সার সংকলনে সীমাবদ্ধ ছিল, তা বঙ্কিম প্রতিভার স্পর্শে প্রাণের স্পন্দনে আন্দোলিত ও জীবনের বহুমুখী উদ্বেলতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। জ্ঞানপ্রধান প্রবন্ধ ভাবপ্রধান রসরচনার রূপ গ্রহণ করেছিল।
গ্রন্থসম্ভার
(1) দর্শন ও ধর্ম বিষয়ক : ‘কৃষ্ণচরিত্র’ (১৮৮৬), ‘ ধর্মতত্ত্ব’ (১৮৮৮)।
জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ: ‘বিজ্ঞানরহস্য’ (১৮৭৫), ‘সাম্য’ (১৮৭৯), ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ (প্রথম-১৮৮৭, দ্বিতীয়-১৮৯২)।
(2) হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ: ‘লোকরহস্য’ (১৮৭৪), ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ (১৮৭৫), ‘মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত’ (১৮৮৪)।
(3) সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ: ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’, ‘শকুন্তলা- মিরন্দা-দেসদিমনা’, ‘ঈশ্বর গুপ্ত’, ‘দীনবন্ধু মিত্র’।
ভাষাশৈলীর বৈশিষ্ট্য
বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের একজন ধ্রুপদি শিল্পী। তিনি বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বন করে প্রবন্ধরচনা করেছেন। তাঁর গদ্যরীতি যেমন প্রাঞ্জল তেমনি রসাস্বাদী ও মনোহর।
(১) বঙ্কিমের সাধু গদ্যরীতি বঙ্কিমী রীতি নামে প্রচলিত। সাধু গদ্যরীতির সুন্দর, সুসংবদ্ধ, অভিজাত, অভিনব প্রয়োগ ও ব্যবহার তাঁর গদ্যকে চমৎকারিত্ব দান করেছে। (২) বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা গদ্য পেল যৌবনমুক্তির এক স্বতঃস্ফূর্ত হিল্লোল। বাংলা গদ্যের বিবর্তনশীলতাকে সেজন্য তিনি সম্মান জায়িয়েছেন। গতিভঙ্গি, শব্দবিন্যাস রীতিবৈশিষ্ট্য পরবর্তীতে আত্মপ্রত্যয় ও রসরুচি ভেদে রূপান্তরিত হয়েছে। (৩) নির্মল হাস্যরস ও তীক্ষ্ণধার দৃষ্টি তাঁর প্রবন্ধে প্রাণ পেয়েছে ভাষা ও ভাবনার মেলবন্ধনে। (৪) সরল মন্তব্যের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তিনি। (৫) বিষয় অনুসারে ভাষা ব্যবহারের রীতি এবং সেই অনুযায়ী বাক্যগুলির দীর্ঘ বা হ্রাসকরণ ঘটিয়ে, হ্রস্ব বাক্যগুলিকে করে তুলেছেন দ্রুতচারী। (৬) আলোচনা ও সমালোচনায় সমৃদ্ধ বঙ্কিম প্রবন্ধ। অনুচ্ছেদের প্রথম ভাগে যা প্রতিফলিত, পরবর্তীতে সেই বিষয় সম্প্রসারিত হয়েছে। (৭) বঙ্কিমের গদ্যের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল পরিহাস প্রবণতা। পরিহাস গুণে গুরুগম্ভীর বিষয়কেও তিনি সরল, প্রাঞ্জল এবং উপাদেয় করে তুলেছেন। (৮) সংস্কৃত শব্দকে তিনি বাংলায় স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করেছেন।
১৪। প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভার মূল্যায়ন করো।
অথবা,
‘রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ।’-অতুলচন্দ্র গুপ্তের এই মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।
সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় যাঁর অবাধ বিচরণ, যাঁর কলমের ছোঁয়ায় মণিমুক্তার জন্ম হয়েছে-তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রবন্ধে রূপগত ও রসগত-এই নতুন দুটি দিক লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রবন্ধ মহাকবির জ্যোতির্ময় কিরণসম্পাতে সমুদ্ভাসিত। তাঁর প্রবন্ধের পরিধি বিস্তৃত এবং রূপবৈচিত্র্য বিস্ময়কর। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলিকে বিষয় আঙ্গিক অনুসারে নিম্নরূপ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে-
(1) ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ: ‘প্রাচীন সাহিত্য’ (১৯০৭), ‘লোকসাহিত্য’ (১৯০৭) ও ‘আধুনিক সাহিত্য’ (১৯০৭), ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ (১৯০৯), ‘সাহিত্যের পথে’ (১৯৩৬), ‘ছন্দ’ (১৯৩৬), ‘সাহিত্যের স্বরূপ’ (১৯৩৭), ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’ (১৯৩৮), প্রভৃতি।
(2) স্বদেশ ও সমকালীন সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ: ‘আত্মশক্তি’ (১৯০৫), ‘ভারতবর্ষ’ (১৯০৬), ‘রাজাপ্রজা’ (১৯০৮), ‘স্বদেশ’ (১৯০৮), ‘কালান্তর’ (১৯৩৭), ‘সভ্যতার সংকট’ (১৯৪১) প্রভৃতি।
(3) শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ: ‘শিক্ষা’ (১৯০৮), ‘শিক্ষার মিলন’ (১৯২১), ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ’ (১৯৩৩), ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ (১৯৪৯), ‘বিশ্বভারতী’ (১৯৫১)।
(4) পত্রজাতীয় ভ্রমণাত্মক রচনা: ‘য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র’ (১৮৮১), ‘ঘুরোপ যাত্রীর ডায়েরী’ (প্রথম-১৮৯১, দ্বিতীয়-১৮৯৩), ‘ছিন্নপত্রাবলী’ (১৯১২), ‘জাপানযাত্রী’ (১৯১৯), ‘রাশিয়ার চিঠি’ (১৯৩১), ‘পথের সঞ্চয়’ (১৯৩৯)।
(5) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ: ‘পঞ্চভূত’ (১৮৯৭), ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ (১৯০৭), ‘ভারতপথিক রামমোহন’ (১৯৩৩)।
(6) জীবনী জাতীয়: ‘জীবনস্মৃতি’ (১৯১২), ‘ছেলেবেলা’ (১৯৪০)।
(7) আধ্যাত্মিক বিষয়ক প্রবন্ধ: ‘ধর্ম’ (১৯০৯), ‘শান্তিনিকেতন’ (১৯০৯-১৯১৬), ‘মানুষের ধর্ম’ (১৯৩৩) প্রভৃতি।
মন্তব্য
বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁর সৃষ্টি প্রয়াস অভিনব। বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য্যে, বৈচিত্র্যে, প্রকাশভঙ্গির বাবৈদগ্ধতায় আর আভিজাত্যপূর্ণ শিল্প মাহাত্ম্যে তাঁর প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ভ্রমণসাহিত্য, ডায়েরি-এইসব বিচিত্রমুখী রচনায় তথ্যকে খুব বেশি প্রাধান্য না-দিয়ে নিজের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন কাব্যিক হৃদয়ে। প্রবন্ধের সর্বত্রই বিরাজিত মহাকবির মনের ছাপ। সর্বত্র মহাকবির বাবৈভব। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ান্তরের স্পর্শে অদ্ভুত ঐক্যের আলোর রোশনায় রবীন্দ্রপ্রবন্ধ ভাস্বর। এমনকি রবীন্দ্রনাথের হাতে সমালোচনা সাহিত্যও সৃষ্টিশীল সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। ‘লিপিকা’-য় কাব্যধর্মী গদ্যের আবিষ্কার গদ্য-প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় অভিনব সংযোজন। বাংলা গদ্যের শক্তি, সীমা ও সহিষ্ণুতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যত পরীক্ষা করেছেন এমন আর কেউ করেননি। এইসব পরীক্ষা চালাতে গিয়ে পর্বে পর্বে তিনি নূতন গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছেন। (‘বাঙ্গালা গদ্যের পদাঙ্ক’/প্রমথনাথ বিশী)।
১৫। প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লেখো এবং তাঁর গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য লেখো।
‘সবুজপত্র’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং কথ্যরীতি বীরবলী ভঙ্গির গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী। তিনি মনে করতেন লেখার ভাষাতে প্রাণসঞ্চার করতে হলে মুখের ভাষার সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভব নয়। বাবৈদ্য, নির্মল পরিহাস, বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকরস ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গির দ্বারা বাংলা গদ্যের বৈচিত্র্য তিনি বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর চিন্তা, মনন ও প্রকাশভঙ্গির বক্রতা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী করে রাখবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর রচনায় ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবই মূর্ত হয়ে উঠেছে।
বিচিত্র গদ্য ও প্রবন্ধগ্রন্থ সম্ভার
‘তেল-নুন-লকড়ী’ (১৯০৬), ‘বীরবলের হালখাতা’ (১৯১৭), ‘নানাকথা’ (১৯১৯), ‘আমাদের শিক্ষা’ (১৯২০), ‘দু-ইয়ারকি’ (১৯২১), ‘বীরবলের টিপ্পনী’ (১৯২১), ‘রায়তের কথা’ (১৯২৬), ‘নানা চর্চা’ (১৯৩২), ‘বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়’ (১৯৩৪), ‘ঘরে বাইরে’ (১৯৩৬), ‘প্রাচীন হিন্দুস্থান’ (১৯৪০), ‘আত্মকথা’ (১৯৪৬), ‘প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু মুসলমান’ (১৯৫৩)।
গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য
(১) প্রমথ চৌধুরীর রচনায় চলিত গদ্যের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশি ও বিদেশি শব্দের বৈদ্যপূর্ণ মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। (২) ব্যঙ্গ ও পরিহাস রসিকতাপূর্ণ রচনা যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনই স্বদেশের নানা সমস্যার কথাও তাঁর বহু প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। (৩) বিষয় উপস্থাপনে যুক্তিবোধের প্রাবল্য। (৪) লঘুগুরু যে-কোনো বিষয়ের ভাবভাবনার প্রকাশে চলিতভাষাকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছেন। (৫) তাঁর গদ্যের ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘ইস্পাতের ছুরি’। তিনি আঙ্গিকের কাঠিন্যতা থেকে প্রবন্ধসাহিত্যকে মুক্তি দিয়েছেন। প্রবন্ধে তিনি বিষয় নিয়ে খেলা করেছেন। খেলার আনন্দ উপভোগ করেছেন। মুখের কথাকে তিনি শিল্পকলায় রূপান্তরিত করেছেন। (৬) কথকতা-সুলভ ভঙ্গি, চলিতভাষা প্রয়োগ, বাবৈদগ্ধ্যতা, ব্যঙ্গ ও পরিহাস প্রবণতা তাঁর গদ্যসাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।